
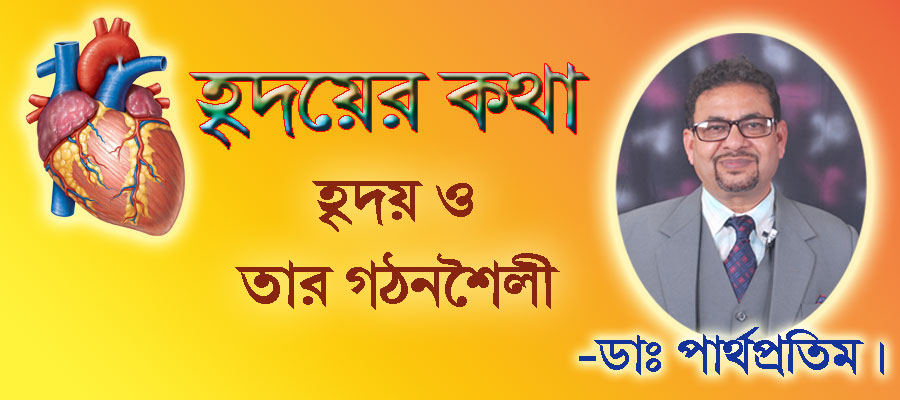
হৃদয়ের কথা- ১ পর্ব-হৃদয় ও তার গঠনশৈলী
এ এক অতন্ত্র প্রহরী। জীবন-মৃত্যুর লাইন অব্ কন্ট্রোলে দাঁড়িয়ে অবিশ্রামভাবে মার্চ করে চলেছে ধুক্-পুক্- ধুক্-পুক্। শুধু জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্তই নয়, জন্মের পূর্বে মাতৃগহ্বরে থাকাকালীন শুরু হয়ে যায় হৃদয়ের কাজ কারবার।
সে এক সূদর অতীতের কথা। তখন কোনো মানবশিশুই ধরার বুকে ধরা দেয়নি। বিবর্তনের সিঁড়ি বেয়ে পৃথিবীতে এসেছে- কেঁচো, জোঁক প্রভৃতি অ্যানিলিডা বা অঙ্গুরীমাল প্রাণীরা। জীববিজ্ঞানীরা এই সময়কে ক্যামব্রিয়ান যুগ (Cambrian) বলে অ্যাখ্যা দিয়েছেন। কেঁচোর পৃষ্ঠীয় ও অঙ্কদেশে বয়ে যাওয়া একজোড়া রক্তনালীকে পাশাপাশিভাবে যুক্ত করেছে চারটি স্পন্দনশীল রক্তথলি। বাইরের পরিবেশের অক্সিজেন কেঁচোর ভেজা ত্বকের মধ্য দিয়ে ব্যাপন প্রক্রিয়ায় মিশে যায় রক্তে, সেই অক্সিজেনপূর্ণ রক্ত শাখানালী ও জালকের পথ ধরে ছড়িয়ে পড়ে তার সারাদেহে। দেহের পাশ বরাবর থাকা স্পন্দনশীল থলির মতো রক্তনালীকে হৃৎপিন্ডের আদিম রূপ বলা যেতে পারে।
প্রাণীর বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে জটিল থেকে জটিলতর হয়েছে তার দেহ গঠন। দেহের প্রতিটি সজীব কোষে খাদ্য, অক্সিজেন পৌঁছে দেওয়া এবং কার্বন- ডাই অক্সাইড ও বিভিন্ন বিপাকজাত পদার্থকে দেহের বাইরে নিয়ে যাওয়ার জন্য ক্যুরিয়ার সার্ভিসের ভূমিকা পালন করে চলেছে তরল যোগকলা রক্ত। হৃৎপিন্ড হলো রক্তনালী- জালকের সুবিশাল পাইপলাইনের একমাত্র পাম্পহাউস।
মানুষের হৃৎপিন্ডটি রয়েছে দু’টি ফুসফুসের মাঝে। একটু বাঁ-দিক ঘেঁষে। বুকের গহ্বরের মধ্যে যে ডায়াফ্রাম বা মধ্যচ্ছদা আছে হৃৎপিন্ড তার ওপরে থাকে। বয়স ও দেহের আকার-আয়তন অনুসারে মানুষের হৃৎপিন্ডের আয়তন নির্ভর করে। কোনো ব্যক্তি মোটা-লম্বা-বেঁটে-রোগা যাই হোক না কেন, তবে মোটামুটিভাবে তার হৃদয়ের আয়তন তার হাতের মুঠোর সমান। অর্থাৎ ঘুঁষি মারার মতো করে হাতের আঙ্গুলগুলিকে মুঠো করলে, কবজি থেকে হাতের তালুর আকার থেকে ব্যক্তির হৃৎপিন্ডের একটি মোটামুটি মাপ পাওয়া যায়। গড় হিসাব থেকে জানা গেছে একটি পূর্ণবয়স্ক মানুষের হৃৎপিন্ডটি ১২-১৩ সেমি. লম্বা ও ৯-১০.৫ সেমি. চওড়া হয়। পূর্ণবয়স্ক পুরুষের হৃদযন্ত্রের ওজন ৩০০ গ্রাম অর্থাৎ তার দেহের মোট ওজনের ২১৫ ভাগের একভাগ। স্ত্রীলোকের হৃৎপিন্ড সে তুলনায় কিছুটা হালকা ২২০ গ্রাম অর্থাৎ মোট দেহ ওজনের ২৫০ ভাগের একভাগ। এদিক থেকে পুরুষেরা নিজেদের বড়ো হৃদয়ের মানুষ বলে দাবি করতে পারেন।
আসুন এবারে গ্রিনেস বুক অব্ রেকর্ডস-এর পাতায় একবার চোখ রাখি। আমেরিকা যুক্তরাষ্টের সারা নাউসা বিশ্বের সবচেয়ে বৃদ্ধ মহিলা। ১৮৮০ সালের ২৪ শে সেপ্টেম্বর তাঁর জন্ম। নেপালের সানসারি জেলার বীর নারায়ণ চৌধুরি মাঝি এতদিন বিশ্বের সবচেয়ে বৃদ্ধ পুরুষ বলে গণ্য হতেন। ১৯৯০ সালের এপ্রিল মাসে ১৪১ বছর বয়সে তিনি মারা যান। বয়োবৃদ্ধ ভারতীয়দের মধ্যে রয়েছেন ত্রিপুরার বিদ্যামোহন দেববর্মা (১৩৭ বছর)। ১৮৬০ সালে তাঁর জন্ম বলে তিনি দাবি করেছেন।
এসব তো গেল অন্য প্রসঙ্গ। এবার আসল কথায় আসা যাক। মাতৃজঠরে ভ্রুণের বয়স যখন ৫ সপ্তাহ তখন থেকেই হৃদযন্ত্র গড়ে উঠতে থাকে। আর ভ্রুণের বয়স ৮ বা ৯ সপ্তাহ হলেই হৃদযন্ত্র তার কাজ শুরু করে দেয়। এই কাজ চলে মৃত্যু পর্যন্ত। সে দিক থেকে দেখতে গেলে এইসব দীর্ঘজীবী মানুষের হৃদয়ের কার্যকাল তাদের জীবদ্দশা থেকে আরো ৩৬ সপ্তাহ বেশি।
বর্তমানে বিজ্ঞানের চমকপ্রদ উন্নতি ঘটলেও আধুনিক প্রযুক্তিবিদেরা এমন কোনো যন্ত্র বা পাম্প উদ্ভাবন করতে পারেন নি যা এত দীর্ঘ সময় ধরে অবিরামভাবে কাজ করে যেতে পারে। আমাদের হৃদয় হলো এমন একটি যন্ত্র যা শুধু সাধারণ মানুষের কাছে নয়, শরীরতত্ত্ববিদরের কাছেও এক বিস্ময়।
হৃদয়ের এই অনন্য কার্যকারিতার পেছনে তার সুস্থির গঠনশৈলী। হৃৎপিন্ড তৈরি হয় এক বিশেষ ধরনের পেশিকলা দিয়ে। প্রাণীরা সারা দেহে একমাত্র হৃদয়েই এই পেশির দেখা মেলে। তাই একে হৃৎপেশি (Cardiac Muscle) বলে। হৃৎপেশির বৈশিষ্ট্য হলো এর তন্তুগুলি আকারে খুব ছোটো। প্রতিটি পেশিতন্তুর চারপাশে যে পাতলা আবরণ বা সার্কোলিমা (Sarcolemma) থাকে; হৃৎপেশির ক্ষেত্রে তা অস্পষ্ট ও অসম্পূর্ণ। এই পেশিকোষের কেন্দ্রে থাকে একটা বড়ো নিউক্লিয়াস। হৃৎপেশি অন্যসব পেশির মতো কিছুক্ষণ কাজ করার পর অবসাদগ্রস্থ হয় না। হ্যাঁ, এই পেশি কোনো অবস্থাতেই প্রাণীর ইচ্ছাধীন নয়। আমরা চাই বা না -চাই আমাদের হৃদয় কিন্তু আপন ছন্দে কাজ করেই চলেছে। ছোট্ট করে বলতে গেলে- আমাদের হৃৎপিন্ড বা হার্ট রক্ত সঞ্চালন প্রক্রিয়ার জন্য চাপ সৃষ্টিকারী, মাংসল, ফাঁপা বিভিন্ন প্রকোষ্ঠে বিভক্ত, স্পন্দনশীল একটি প্রধান কেন্দ্রীয় যন্ত্র।
হৃদযন্ত্রের দেওয়াল তিনস্তরের পেশি দিয়ে তৈরী। সবচেয়ে ভেতরে যে স্তরটি থাকে তার নাম এন্ডোকার্ডিয়াম (Endocardium)। এটি বাম অলিন্দে সবচেয়ে পুরু ও নিলয়ে পাতলা। মাঝের স্তরটিকে বলে মায়োকার্ডিয়াম (Myocardium)। মায়োকার্ডিয়াম হৃদযন্ত্রে গুরত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সবচেয়ে বাইরের স্তরটি হচ্ছে পেরিকার্ডিয়াম (Pericardium)। এটি একজোড়া পাতলা চাদরের মতো আচ্ছাদন। চাদর দু’টির মাঝে থাকে এক ধরনের জলীয় পদার্থ যাকে বলে পেরিকার্ডিয়াল ফ্লুইড (Pericardial Fluid)।
হৃদযন্ত্রের মধ্যে চারটি প্রকোষ্ঠ রয়েছে। এর মধ্যে দু’টি অলিন্দ ও দু’টি নিলয়। অলিন্দ দু’টির মাঝে যে প্রাচীর থাকে তাকে বলে আন্তঃ নিলয় প্রাচীর বা ইন্টার অ্যাট্রিয়াল সেপ্টাম (Inter Atrial Septum)| । একইভাবে আন্তঃ নিলয় প্রাচীর বা ইন্টার ভেন্টিকিউলার সেপ্টাম (Inter Ventricular Septum) ডান ও বাম নিলয়ের মাঝে দেওয়ালের মতো থাকে। হৃৎপিন্ডের মধ্যে বাম নিলয়ই সবচেয়ে পেশিবহুল। হৃদযন্ত্রের ভেতর রয়েছে কতগুলি ভালভ বা কপাটিকা। এই ভালব্গুলির জন্য রক্ত শিরা ধমনীর সড়ক দিয়ে সবসময় একই দিকে যায়। অর্থাৎ ‘ইধার কা মাল উধার’ হতে পারে। তবে কখনই ‘উধার কা মাল ইধার’ হবেনা। বাম অলিন্দ ও বাম নিলয়ের মাঝে যে ছিদ্র আছে সেখানে থাকে দুই পাল্লাওয়ালা কপাট মাইট্রাল ভাল্ভ (Mitral Valve)। এই দরজায় দু’টি পাল্লা থাকে ব’লে এর আর এক নাম বাইকাসপিড ভাল্ভ (Bicuspid Valve)। অলিন্দ থেকে রক্ত নিলয়ে আসে তবে নিলয় থেকে রক্ত অলিন্দে যেতে পারে না। ডান হৃৎপিন্ডের অলিন্দ বা নিলয়ের মাঝে একই রকম কপাটিকা থাকে তবে এটাতে তিনটি পাল্লা রয়েছে। তাই এর নাম ট্রাইকাসপিড ভাল্ভ (Tricuspid Valve)।
বাম নিলয় থেকে অক্সিজেন ভরা বিশুদ্ধ রক্ত মহাধমনী বা অ্যাওর্টার ভেতর দিয়ে মানব শরীরে ছড়িয়ে পড়ে। আবার ডান নিলয় থেকে কার্বন-ডাই অক্সাইড পূর্ণ দূষিত রক্ত পালমোনারি বা ফুসফুসীয় ধমনীর সাহায্যে ফুসফুসে চলে যায়। এই দুই ধমনীর মুখে থাকে অষ্টমীর চাঁদের মতো দু’টি কপাটিকা বা সেমিলুনার ভাল্ভ (Semilunar Valve)। এরা ধমনীতে প্রবাহিত রক্ত নিলয়ে ফিরে আসতে বাধা দেয়। মহাধমনীর মুখে যে কপাটিকা আছে তার নাম অ্যাওর্টিক ভাল্ভ ও ফুসফুসীয় ধমনীর ভালভ বলে পালমোনারি ভালভ।
হৃদয়ের সংকোচন-প্রসারণের ফলে প্রায় ৫ থেকে ৬ লিটার রক্ত প্রতি মিনিটে অলিন্দে আসে। ঐ পরিমাণ রক্ত আবার নিলয় থেকে বের হয়ে যায়। স্বাভাবিকভাবে মিনিটে যে পরিমাণ রক্ত প্রবাহিত হয় তা হলো-
| মস্তিষ্ক (Brain) | ৭০০-৮০০ মিলি লিটার |
| হৃৎপিন্ড (Heart) | ২০০-২১০ মিলি লিটার |
| যকৃৎ (Liver) | ১৫০০-১৭০০ মিলি লিটার |
| বৃক্ক ( Kidney) | ১৩০০-১৫০০ মিলি লিটার |
| বিভিন্ন পেশিতে (Muscles) | ৬০০-৯০০ মিলি লিটার |
হৃৎপিন্ড নামক পাম্প হাউসে প্রতি নিয়ত চলছে- সংকোচন ও প্রসারণ। হৃৎপেশির এই চুপসে যাওয়া ও প্রসারিত হওয়াকে বলে হৃৎস্পন্দন (Heart Beat)। এক মিনিটে হৃৎপিন্ড যতবার স্পন্দিত হয় তাকে হৃৎস্পন্দনের হার বা হার্টরেট (Heart Rate) বলে।
বিভিন্ন বয়সে হৃৎস্পন্দনের হার বিভিন্ন হয়-
| গর্ভাবস্থায় ভ্রুণের (২৪ সপ্তাহ) | ১৪০-১৬০ |
| জন্মের পর শিশুর | ১৩০-১৪০ |
| ১ মাস বয়স্ক শিশুর | ১২০-১৩০ |
| ১ বছরের শিশুর | ১১৫-১২০ |
| ৩ বছরের শিশুর | ৮০-১০০ |
| ১২ বছর বয়সে | ৭০ |
| যৌবনে | ৮০-৮৫ |
| মধ্য বয়সে | ৭০-৭৫ |
| বৃদ্ধ বয়সে | ৬০-৬৫ |
সুতরাং এটা বোঝা যাচ্ছে যে, মাতৃজঠরে থাকাকালীন হার্টরেট যা থাকে; বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে স্বাভাবিকভাবে তা কমে আসে।
বিভিন্ন কারণে হৃৎস্পন্দনের হার পরিবর্তিত হয়। যেমন- মানসিক উত্তেজনা, ব্যায়াম ও শারীরিক পরিশ্রমে বিপাকের হার অর্থাৎ দেহের সঞ্চিত শক্তি ক্ষয়ের মাত্রা বেড়ে যায়। তাই সে কারণে বেড়ে যায় হার্টরেট। অন্যদিকে বিশ্রাম ও ঘুমের সময় বিপাক হার কম হওয়ার জন্য হৃৎস্পন্দনের গতি কমে আসে। কোনো কারণে শ্বাসপ্রশ্বাসের হার বাড়লে হার্টরেট বেড়ে যায়। দেহের আকৃতির (Size) সঙ্গে হৃৎস্পন্দনের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে। দেখা গেছে, যে প্রাণীর আকৃতি যত বড়ো তার হার্টরেট তত কম। পূর্ণবয়স্ক হাতির ক্ষেত্রে তা প্রতি মিনিটে ২৫ বার। অন্যদিকে নেংটি ইঁদুরের (Mouse) প্রতি মিনিটে পাঁচশো বার। সাধারণ মানুষের তুলনায় জাপানি সুমো কুস্তিগীরদের হার্টরেট অনেক কম থাকে।
খেলোয়ারদের হার্টরেট বেশ কম থাকে। অনেকে বলেন- এর মধ্যেই লুকিয়ে আছে তাদের সাফল্যের চাবি। প্রচলিত কথায় একে বলে ‘অ্যাথিলেট পালস। দৌড়বিদ্ রজার ব্যানিস্টার, এমিল জেটোপেকের মাত্র ২৫ বার প্রতি মিনিট। ফুটবল সম্রাট পেলের ছিল ৩৭। আমাদের সোনার মেয়ে জ্যোর্তিময়ী ৪১। স্বাভাবিকভাবে পালস রেট কম হওয়ার জন্য তারা অতিরিক্ত পরিশ্রম ও উত্তেজনার সময় হাঁফিয়ে ওঠেন না।
দেহের তাপমাত্রা হ্রাস-বৃদ্ধির সঙ্গে হৃৎস্পন্দনের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে। জ্বর বা অন্য কোনো কারণে দেহের তাপমাত্রা বাড়লে, প্রতি ডিগ্রি ফারেনহাইটের জন্য স্বাভাবিক অবস্থার চেয়ে ৮-১০ বার হার্টরেট বেড়ে যায়।
পূর্ণবয়স্ক মানুষের ক্ষেত্রে দেহের তাপমাত্রা ও হৃৎস্পন্দনের
সম্পর্ক হল-
৯৮ ডিগ্রি জ্বরে হার্টরেট ৬২ বার
৯৯ ডিগ্রি জ্বরে হার্টরেট ৭০ বার
১০০ ডিগ্রি জ্বরে হার্টরেট ৮০ বার
১০১ ডিগ্রি জ্বরে হার্টরেট ৯০ বার
১০২ ডিগ্রি জ্বরে হার্টরেট ১০০ বার
১০৩ ডিগ্রি জ্বরে হার্টরেট ১১০ বার
১০৪ ডিগ্রি জ্বরে হার্টরেট ১২০ বার
১০৫ ডিগ্রি জ্বরে হার্টরেট ১৩০ বার
১০৬ ডিগ্রি জ্বরে হার্টরেট ১৩৮ বার
হাতের কাছে থার্মোমিটার না থাকলে রোগীর পালস রেট গুণে তার জ্বরের তীব্রতা সম্বন্ধে কিছুটা আঁচ করতে পারবেন। কারো কারো ক্ষেত্রে হৃৎস্পন্দনের গতি সবসময় স্বাভাবিক অবস্থার চেয়ে দ্রুততর থাকে। ডাক্তারি শাস্ত্রে এই লক্ষণকে বলে ট্যাকিকার্ডিয়া (Tachycardia)। এই রোগীর হার্টরেট ১০০ থেকে ২০০ বারও হতে পারে। ট্যাকিকার্ডিয়ার পেছনে বিভিন্ন কারণ দেখা যায়। হৃৎপেশীর প্রদাহ (Myocarditis), হৃৎপিন্ডের আকার বড়ো হয়ে যাওয়া (Hypertrophy of Heart) রক্তবাহী ধমনী পুরু হয়ে যাওয়া (Arterial sclerosis), হৃৎপিন্ডের ভেতরের আবরণের অসুস্থতা (Endocarditis) আরো বহু কারণে এই লক্ষণ দেখা যায়।
আবার অনেকের ক্ষেত্রে হৃৎস্পন্দনের গতি অনেক কম হয়। এমন কি মিনিটে ৫০ থেকে ৩০ বার হয়ে থাকে। একে ব্র্যার্ডিকার্ডিয়া (Bradicardia) বলে। ফুসফুসের বায়ুকোষস্ফীতি (Emphysema), নেফ্রাইটিস বা ইউরিমিয়া প্রভৃতি প্রস্রাব যন্ত্রের রোগ, রক্তে হিমোগ্লোবিনের ঘাটতি এইসব বহু কারণে ব্র্যাডিকার্ডিয়া হতে পারে। তবে এমনও দেখা গেছে যে অনেকের হৃৎস্পন্দন সারাজীবন অতি দ্রুত বা ধীর গতিতে চললেও কোনো বিশেষ রোগে তারা আক্রান্ত হন নি।
আমাদের হৃৎপিন্ডের সংকোচন ও প্রসারণের সময় চাপের পরিবর্তন ঘটে। এরই ফলে অপ্রত্যক্ষভাবে রক্তনালীর দেওয়ালের বিস্তৃতি (Expansion) ও লম্বমান (Elonagtion) হওয়াকে সাধারণভাবে নাড়ী (Pulse) বলা হয়। হাতের কব্জির কাছে বুড়ো আঙ্গুলের দিকে যে রেডিয়াল ধমনী (Radiel Artery) থাকে তার ওপর তর্জনী, মধ্যমা, ও অনামিকার সাহায্যে অল্প চাপ দিয়ে নাড়ী পরীক্ষা করা হয়। ধমনীর স্পন্দন কপালের দু’পাশে, গলায় ও আরো কয়েকটি অংশে পাওয়া গেলেও কব্জিতে নাড়ী দেখার সুবিধা বেশি, এখানে রেডিয়াল আর্টারি চামড়ার ঠিক নিচেই থাকে। পুরুষের ডান হাতে ও মহিলাদের বাম হাতের নাড়ী দেখাই ডাক্তারি রীতি। নাড়ী পরীক্ষার সময়- প্রতি মিনিটে নাড়ীর স্পন্দন কতবার হচ্ছে, নাড়ীর স্পন্দন সমান সময়ের ব্যবধানে হচ্ছে কী না এসবের প্রতি ডাক্তারবাবুরা লক্ষ্য রাখেন।
মানবদেহের সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গের কাজ-কারবার নিয়ন্ত্রণ করার চাবিকাঠি রয়েছে তার মস্তিষ্কে। আমাদের হৃদযন্ত্রের কাজকর্ম পরিচালনার জন্য মস্তিষ্কের মেডুলা (Medulla) অংশের মধ্যে রয়েছে একটি হৃদয় নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্র (Cardiac center)। এই অংশটি আবার দু’টি ভাগে বিভক্ত- কার্ডিয়ো এক্সিলারেটার সেন্টার (Cardio accelerator center) ও কার্ডিয়ো ইনহিবিটার সেন্টার (Cardio inhibitor center)। এক্সিলারেটার সেন্টার সিমপ্যাথেটিক নার্ভের (Sympathetic) সাহায্যে হার্টরেট বাড়াতে চেষ্টা করে। অন্যদিকে ইনহিবিটার সেন্টার ভেগাস নার্ভের (Vagus) মাধ্যমে হৃৎস্পন্দনের হার কমাতে চায়। এইভাবে সিমপ্যাথেটিক ও ভেগাস নার্ভের মিলিত প্রচেষ্টার ফলেই সুস্থ- স্বাভাবিকভাবে সুনির্দিষ্ট তালে চলতে থাকে হৃদয়ের স্পন্দন ঊষালগ্ন থেকে জীবন গোধূলির অভিমুখে।